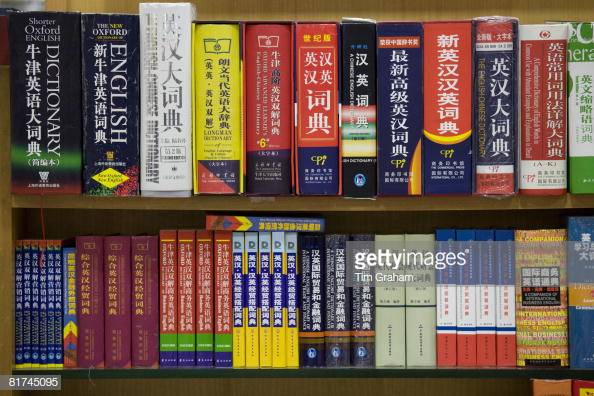
মানব সভ্যতা ও সমাজের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে মূলত ভাষা। নিজেদের মধ্যে অর্থপূর্ণভাবে ঠিক করে যোগাযোগ করতে না পারলে এই সভ্যতা গড়ে তোলা আদৌ সম্ভব হতো বলে মনে হয় না। অন্যান্য প্রাণীর দিকে তাকালেই এটা আমরা বুঝতে পারি।
এই ভাষার প্রচলন কীভাবে হলো সেটা নিয়ে অনেক গল্প আছে। এরকম বিখ্যাত গল্পগুলোর একটি আমরা প্রায় সবাই সম্ভবত ছোটকালে পড়েছি বা শুনেছি। বিশেষ করে ব্যাকরণ বইগুলোতে এই গল্পটা থাকত। তবে এই গল্পটা সরাসরি ভাষার উৎপত্তি নিয়ে না, বরং বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি নিয়ে।
গল্প মতে, প্রাচীন ব্যবিলনের মানুষ ভেবেছিল একটা টাওয়ার বানাবে। সেই টাওয়ার দিয়ে ছুঁয়ে ফেলবে আকাশ। মানুষ ভাবত, নীল আকাশের ওপারেই স্রষ্টার বাস। তাই টাওয়ার বানালে স্রষ্টার কাছে সরাসরি পৌঁছানো যাবে, কথা বলা যাবে। কিন্তু টাওয়ারের কাজ অনেক দূর হওয়ার পরে স্রষ্টা ভাবলেন, এভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না!
একদিন লোকজন ইট-পাথর আনতে গিয়েছিল। টাওয়ারের কাছে এসে ওরা টের পেল, কেউ আর কারো কথা বুঝতে পারছে না। স্রষ্টা আসলে একেকজনকে একেক ভাষা শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেউ কথা না বুঝলে টাওয়ারের কাজ কীভাবে এগোবে! ভেস্তে গেল টাওয়ার বানানো। স্রষ্টা আকাশের ওপারে অধরাই রয়ে গেলেন। আর এদিকে, মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল নানা ধরনের ভাষা।
এই গল্পের অনেক ফাঁক-ফোঁকর আছে। চাইলেই গল্পটা নিয়ে নানারকম প্রশ্ন করা যায়। কিন্তু সেসব প্রশ্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য না। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, এই ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখা। বুঝতে চেষ্টা করা, আসলেই ঠিক কী হয়েছিল। তবে এই কাজটা আমরা করব বিজ্ঞানের চোখে, তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে।
সেজন্য অবশ্যই আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রাচীন পৃথিবীতে। যে পৃথিবীর কথা ঘুরে ফিরে এসেছে মানুষের ইতিহাসে, কল্পে-গল্পে।
২
কথা হলো, আমরা কি শুরু থেকেই শুরু করব? চট করে ফিরে যাব সেই পৃথিবীতে? ভাবার চেষ্টা করব, সে সময়ের মানুষ তখন কী করছিল? উঁহু, সেটা করা যাবে না। যুক্তি আমাদের বলে, উল্টো দিক থেকে পুরো জিনিসটা দেখার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। ধীরে ধীরে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ফিরে যেতে হবে সেই সময়টায়, যখন ভাষার শুরু হয়েছিল।
কথা হলো, বিজ্ঞানীরা এটা কীভাবে করেন? মানে, ভাষা তো আর ফসিল রেখে যায়নি যে, ফসিল বিশ্লেষণ করে, কার্বন ডেটিং করে এর ইতিহাস বের করে ফেলা যাবে। কথা সত্য। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের দেহের গঠণ বিশ্লেষণ করলে সেটা দেখা যায় যে, ধীরে ধীরে তারা যোগাযোগের দিকে ঝুঁকছে। তাদের দেহে সেই চিহ্ন ফুটে উঠছে ধারাবাহিকভাবে। সেই সঙ্গে তাদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন জিনিসেও আমরা এর ছাপ দেখতে পাই। এসব সূত্র ধরে ধরেই বিজ্ঞানীরা ভাষার শুরুর গল্পটা বোঝার চেষ্টা করেছেন।
আগেই বলেছি, সেটা করতে হবে উল্টোভাবে। এই হিসেবে, প্রথম প্রমাণটা পাওয়া যায় মানুষের লেখালেখির। যে লিখতে পারে, সে যে ভাষা পারবে, সেটা তো আর আলাদা করে বলে দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মানুষের লেখার ইতিহাসের সূচনা হয়েছে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে। তার মানে, এটা আমাদের খুব বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারে না। সেজন্য উনিশ শতকের বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, ভাষার উৎপত্তি বের করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। শুধু ভেবেই ক্ষান্ত দেননি। ১৮৬৬ সালে প্যারিস ল্যাঙ্গুইস্টিক সোসাইটি এ বিষয় নিয়ে আলোচনা-গবেষণাও নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। উঁহু, গবেষণা করলে পাপ হবে, এমন না। ওদের মনে হয়েছিল, এই নিয়ে কাজ করাটা কেবলই সময় নষ্ট।
আশার কথা হলো, সময় বা অর্থ নষ্ট হবে ভেবে কৌতূহলী মানুষ কখনোই থেমে যায়নি। সেজন্যেই মানুষ চাঁদে পা রাখতে পেরেছে। মানুষের হাতে গড়া মহাকাশযান পেরিয়ে গেছে সৌরজগতের সীমানা। একইভাবে একশ বছরের মতো পরে এসে জীববিজ্ঞানী ও ইভোলিউশনারি থিওরিস্টরা ভাবলেন, এভাবে তো ভাষাকে ফেলে রাখার কোনো মানে হয় না। আমাদের জীবন ও সভ্যতার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইতিহাস জানতে হবে। সেজন্য কাজে নামা দরকার। কিন্তু কীভাবে?
ফসিল নেই, নেই যথেষ্ট সূত্র। লেখালেখিও শুরু হয়েছে অল্প কিছুদিন আগে। তাহলে উপায়? বিজ্ঞানীরা ভাবেন। ভেবে ভেবে তারা সেই আপ্ত বাক্যের কাছে ফিরে গেলেন। দশে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ! শুধু জীববিজ্ঞানের হাত ধরে হয়তো হবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের বাকি সব শাখা আছে কী করতে? শেষমেষ প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষা বিজ্ঞান ও কগনিটিভ সায়েন্স- সব কিছু একসঙ্গে নিয়ে মাঠে নামলেন বিজ্ঞানীরা। অবশেষে ফল পাওয়া গেল৷ এর মধ্যে দিয়ে শুধু একটি নয়, মানুষের ভাষা খুঁজে পাওয়া নিয়ে দু-দুটো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান মিলে গেল একসঙ্গে।
৩
চল্লিশ হাজার বছর আগের কথা। মানুষ তখন গুহাচিত্র আঁকত। এ ধরনের ছবি আমরা দেখেছি। সেসব ছবির পেছনে চিন্তা, সংস্কৃতি ও বিমূর্ত ভাবনা ছিল, এটা আমরা বুঝতে পারি। ভাষার জন্যে তো ঠিক এই জিনিসগুলোই দরকার, তাই না? তাহলে, কয়েক হাজার বছর থেকে চল্লিশ হাজার বছর পর্যন্ত পিছিয়ে এলাম আমরা। কথা হলো, এই সময়েই কি ভাষার আবির্ভাব হয়েছিল?
হতে পারে। না-ও হতে পারে! সহজ কথায়, সবই ঠিক আছে, কিন্তু এককভাবে এই ব্যাখ্যাটি যথেষ্ট না। অর্থাৎ আরো প্রমাণ দরকার। সেজন্যে আমরা সে সময়ের মানব-সমাজের দিকে তাকাতে পারি।
এ সব মিলে ধরে নেওয়া যায়, মানুষের মাঝে ভাষার উদ্ভব হয়েছিল চার লাখ বছর আগে।
মানুষের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখব, চল্লিশ হাজার বছর আগে মানুষ কিন্তু এক জায়গায় নেই। গোত্র বা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে গেছে। তার মানে, এই সময়ে যদি ভাষার উৎপত্তি হয়, তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় একইসঙ্গে বা অল্প সময়ের ব্যবধানে সব মানুষদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসতে হবে। চিন্তার ক্ষমতা তৈরি হলেই শুধু হবে না, সেটা প্রকাশের মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা এবং সেজন্য দেহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও হতে হবে। এ থেকে আমরা একটা যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আসতে পারি।
মানুষ নিশ্চয়ই আরো আগেই ভাষা শিখে গিয়েছিল। সেজন্যই তারা বিমূর্ত চিন্তা করতে শিখেছে এবং সেসব গুছিয়ে আঁকতে শিখেছে গুহার দেয়ালে। তাহলে কী দাঁড়াল ব্যাপারটা? তখনকার পৃথিবীতেও ভাষা ছিল, হয়তো বিভিন্ন গোত্র বা দলের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলত; কিন্তু উৎপত্তিটা তখন হয়নি। হয়েছে আরো আগে, আরো অনেক আদিম পৃথিবীতে।
৪
আদিম পৃথিবীতে মানুষের আগেই এসেছিল এপরা। এই এপদের গলায় বড় আকারের বায়ুথলী ছিল। এটা দিয়ে তারা ‘গোঁ গোঁ’ ধরনের শব্দ করে প্রতিপক্ষ বা অন্যান্য প্রাণীকে ভয় দেখাত। সমস্যা হচ্ছে, এ ধরনের বায়ুথলী স্বরবর্ণের উচ্চারণে বাধা দেয়। এটা কিন্তু বিজ্ঞানীরা ইচ্ছেমতো বলে দেননি। বেলজিয়ামের ফ্রি ইউনিভার্সিটি অফ ব্রাসেলসে বিজ্ঞানী বার্ট দ্য বোর সিমুলেশন করে দেখিয়েছেন। কিন্তু মানুষের ভাষার পেছনে স্বরবর্ণ, যাকে বলে, আবশ্যক।
এপদের মধ্যে এ ধরনের বায়ুথলী ছিল ঠিকই, কিন্তু হোমো হাইডেলবার্জেনিস প্রজাতীর দেহে এরকম কিছু দেখা যায় না। এই হোমো হাইডেলবার্জেনিস থেকেই পরে নিয়ান্ডারথাল ও স্যাপিয়েন্সরা এসেছে বলে ধারণা করেন বিজ্ঞানীরা। হোমো হাইডেলবার্জেনিস পৃথিবীতে ছিল প্রায় সাত লাখ বছর আগে। অর্থাৎ এ সময় পৃথিবীতে ভাষা না থাকলেও, ভাষা তৈরি হওয়ার বেশ কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান ততদিনে চলে এসেছে।
আধুনিক মানুষের কথা যদি ভাবি, মস্তিষ্ক থেকে মেরুদণ্ড হয়ে অনেক অনেকগুলো স্নায়ু ডায়াফ্রাম এবং পাঁজরের মধ্যকার পেশীতে এসে যুক্ত হয়েছে। ঠিকভাবে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও যথার্থ শব্দ করার জন্য এগুলো জরুরি ভূমিকা রাখে। এই একই জিনিস নিয়ান্ডারথালদের মধ্যেও দেখা যায়।
এই দুই প্রজাতির কানের ভেতরের অংশেও একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। ফলে, মানুষের উচ্চারিত শব্দের কম্পাংকের যে পরিসীমা আছে- এই সীমায় প্রজাতি দুটির কানের ভেতরে দারুণ সংবেদনশীলতা তৈরি হয়েছে। কথা বলার জন্য শোনা ও এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝাটা জরুরি। এটার খুব সহজ একটা উদাহরণ আমরা বর্তমানেই দেখতে পারি। যারা কথা বলতে পারেন না, তারা কানেও শুনতে পান না। কারণ, শুনে সেটা প্রকাশ না করতে পারলে, এই ভার মস্তিষ্ক নিতে পারবে না। আবার, না শুনলে বলার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা তৈরি হওয়া একরকম অসম্ভব।
এরপরেও, কথা বলার জন্য আরেকটা জিনিস দরকার। FOXP2 জিন। মস্তিষ্কের যে অংশ কথা নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে কারিকুরি ফলায় এটি। অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যেই এটা থাকে। কিন্তু মানুষের ভেতরে এই জিনটি কিছুটা উন্নত। সেজন্যই আমরা মুখ ও চেহারায় ভাষার জন্য প্রয়োজনীয় নড়াচড়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। নিয়ান্ডারথালদের মধ্যেও এই জিন ছিল, কিন্তু এতটা উন্নত ছিল না।
এসব তথ্য আমাদেরকে একটা সময়ের দিকে ইঙ্গিত করে। এ থেকে বলা যায়, মোটামুটি চার লাখ বছর আগে পৃথিবীতে ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল। ততদিনে মানুষ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনীয় শারীরিক সক্ষমতা চলে এসেছে তার ভেতরে। ধীরে ধীরে চিন্তার ক্ষমতাও বাড়ছে। সেজন্যই এই ভাবনাগুলো প্রকাশ করা জরুরি হয়ে গেছে। ফলে তৈরি হয়েছে ভাষা।
কিন্তু আরো আগে, প্রায় দুই মিলিয়ন বছর আগে হোমো ইরেক্টাসরা যখন শিকার করত, তখন তারা নানারকম যন্ত্র বানাত সেজন্যে। তাহলে তারাও কি ভাষা জানত? হয়তো জানত। হয়তো জানত না। কিন্তু সেই ভাষা যে আধুনিক মানুষের ভাষা ছিল না, এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি নিশ্চিত। মানুষের ভাষার আদিম রূপ, হয়তো ঠিক ভাষা হয়েও ওঠেনি- এমন কিছু থাকলেও থাকতে পারে সে সময়।
এ সব মিলে ধরে নেওয়া যায়, মানুষের মাঝে ভাষার উদ্ভব হয়েছিল চার লাখ বছর আগে। আর, সেই ভাষাই দিনে দিনে আরো পরিণত হয়েছে। আবার, মানুষ দল বা গোত্রে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে বিকৃত হয়ে গেছে ভাষা। সেভাবেই তৈরি হয়েছে নানা ধরনের এত সব ভাষা। কিন্তু যতই আলাদা হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি না কেন, ভালোভাবে খুঁজলে আজও আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মধ্যেও মিল খুঁজে পাই, কাছাকাছি উচ্চারণ ও অর্থের শব্দ খুঁজে পাই। এই সব কিছুই আমাদের একটি সাধারণ ভাষার দিকে ইঙ্গিত করে। সাধারণ এক প্রজাতির ভাষার শুরুটাও যে একটা সাধারণ ভাষা দিয়েই হবে, তা আর আশ্চর্য কী!
৫
ভাষার উদ্ভবের সময়কাল নাহয় পাওয়া গেল। কিন্তু কথা হলো, এই ভাষাটা এলো কীভাবে? ভাষার উৎপত্তি যে যোগাযোগের জন্য, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু এই তাড়নাটা মানুষ অনুভব করা শুরু করল কেন? এই প্রশ্নটাই মানুষের ভাষা খুঁজে পাওয়া নিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন। (প্রথম প্রশ্নটা কী ছিল, সেটা কি আলাদা করে আর বলা লাগবে? তা-ও বলে দেই। প্রশ্নটা হলো, ভাষার উৎপত্তিটা কখন হয়েছিল? আসলে, এই প্রশ্নের উত্তর বের করতে না পারলে, সে সময় মানুষ কী কারণে এই তাড়নাটা অনুভব করেছিল, সেটা বের করা কঠিন।)
এই প্রশ্নের তিনটি সম্ভাব্য উত্তর আছে। প্রথম উত্তরটা দিয়ে গেছেন চার্লস ডারউইন। ভদ্রলোক বলেছিলেন, বিভিন্ন প্রাণীকে সঙ্গী নির্বাচনের কৌশল হিসেবে অদ্ভুত সব কাজকর্ম করতে দেখা যায়। মানুষও সেরকম কিছু করতে চাইত। এর ফলে প্রোটোল্যাঙ্গোয়েজ বা ‘আদিভাষা’ ধরনের একটা কিছু একটা গড়ে ওঠে। অবশ্য, এই আদিভাষার সরাসরি কোনো অর্থ ছিল না। যেমন- পাখিদের ডাক।
পুরুষরা সেই আদিভাষা ব্যবহার করে নারীদের আকর্ষণ করতে চাইত। প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য তারা আদিভাষা নিয়ে আরো ভাবতে থাকে, এবং আরো জটিল ও সুমধুর কোনো ধ্বনি প্রকাশের চেষ্টা করতে থাকে। এভাবেই ভাষা গড়ে ওঠে। ডারউইন উদাহরণ হিসেবে গিবনদের কথা বললেন। এই প্রাইমেটরাও এভাবে গেয়ে গেয়ে নারী গিবনদের আকৃষ্ট করতে চায়। কেউ কেউ পরে এই অনুমানের ওপরে ভিত্তি করে বলেছেন, শুধু পুরুষরাই এমনটা না-ও করতে পারে। নারীরাও হয়তো একইভাবে পুরুষদের আকৃষ্ট করতে চাইত।
কিন্তু এরকম হলে, এর ফলে জন্ম নেওয়া বাচ্চাদের বাকিদের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে থাকার কথা। বাড়তি কোনো বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা পাওয়ার কথা তাদের। আবার, একই জিনিস বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়া সবগুলো গোত্র বা দলের মধ্যেই ঘটতে হবে। এসব কিছু বিবেচনা করে ডারউইনের এই উত্তরকে ঠিক জুতসই মনে হয় না।
কিন্তু এই আইডিয়ার ওপরে ভিত্তি করেই দ্বিতীয় উত্তর বা ধারণাটি গড়ে ওঠে। বিজ্ঞানীরা খেয়াল করে দেখলেন, মানুষ, এমনকি অন্ধরাও সাধারণত হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলার চেষ্টা করে। তাহলে, ‘আদিভাষা’টা হয়তো স্বর নির্ভর না, বরং ভঙ্গিনির্ভর হয়ে গড়ে উঠেছিল। সেই ব্যাপারটাই এখনও আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে। হয়তো সেজন্যই এখনো আমরা কিছু বোঝাতে না পারলে হাত বা কাঁধ নেড়ে অঙ্গভঙ্গি করি। আবার, সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই ভঙ্গি ভালোরকম প্রভাব রাখতে পারে। যেমন- বক্তব্যের সময় মানুষের ভঙ্গি দেখে আকৃষ্ট হই আমরা। নাচের মুদ্রা দেখে আকৃষ্ট হই। এই ব্যাপারগুলোর ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় কিছুটা করে।
আবার খেয়াল করলে দেখা যাবে, অন্যান্য বেশ কিছু প্রাণীও টুকটাক অঙ্গভঙ্গি করে। মানুষ হয়তো ভাবতে শেখার কারণে এই ভঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছিল আরো অনেক দূর। আর, অঙ্গভঙ্গি করে যে পুরোপুরি যোগাযোগ করা যায়, সেটা তো আমরা জানিই। মূক-বধির অনেকেই এভাবে যোগাযোগ করেন।
দারুণ চিন্তা-ভাবনা হলেও, এই প্রস্তাবনারও একটা বড় ঝামেলা আছে। ভঙ্গিনির্ভর এই ভাষা থেকে স্বরনির্ভর ভাষা এলো কীভাবে?
ফলে, তৃতীয় আরেকটি আইডিয়া বা উত্তর নিয়ে ভাবলেন বিজ্ঞানীরা। এই আইডিয়াটিই বর্তমানে সবচেয়ে ভালোভাবে ভাষাকে ব্যাখ্যা করতে পারে। এটাকে বলে ওনোম্যাটোপিয়া (onomatopoeia)। মানে, কোনো শব্দ শুনে সেটাকে নকল করার চেষ্টা। এখনও মানব শিশুদের এরকম শব্দ শুনে শুনে বলার চেষ্টা করতে দেখা যায়।
মানুষের যদি ভাষা বলার মতো যথেষ্ট বোধ না-ও থেকে থাকে, তবু শুনে শুনে এই নকল করতে পারাটা খুব জটিল কিছু না। আগেই বলেছি, ভাষা আসতে আসতে ততদিনে মানুষের মধ্যে ধ্বনি উচ্চারণের শারীরিক সক্ষমতা চলে এসেছে। তাছাড়া, নতুন কিছু গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, অন্যান্য প্রাইমেটও বেশ ভালোভাবেই শ্বাস এবং গলার নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
যৌক্তিকভাবে ব্যাপারটা থেকে আমরা একটা কল্পনা দাঁড় করাতে পারি। বিভিন্ন প্রাণীর ডাক শুনে শুনে মানুষ সেটাকে নকল করতে শিখেছে। সেসব প্রাণীর বিরুদ্ধে টিকে থাকতে গিয়ে বানাতে হয়েছে সরঞ্জাম। সেই সাথে, সেরকম কোনো প্রাণী, যেমন- বাঘকে আসতে দেখলে বাকিদের সাবধান করে দেওয়ার প্রয়োজনীতা তৈরি হয়েছে। বাঘের গর্জন নকল করে নিজেদের লোকজনকে সতর্ক করে দেওয়ার চেয়ে সহজ আর কী আছে? তাতে করে ভিন্ন ভিন্ন প্রানিকে শনাক্ত করতে পারছে মানুষ। আবার, ধীরে ধীরে এসব ধ্বনি বা ডাকের মধ্যে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে। আরেকটা ভালো ব্যাপার হলো, বিভিন্ন প্রাণির ডাক নকল করে শিকারের জন্য তাদেরকে প্রলুব্ধ করে ফাঁদেও ফেলা সম্ভব ছিল। এভাবে ধীরে ধীরে অর্থবোধক ধ্বনি বুঝতে শিখেছে মানুষ। বুঝতে শিখেছে, ধ্বনির মাধ্যমে চাইলে অন্যদেরকে কিছু বোঝানো যায়।
সেই সাথে অঙ্গভঙ্গিও শিখছিল মানুষ। এটা অবশ্য অনেকটাই সহজাত (মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও এটা দেখা যায়)। তাছাড়া, সরঞ্জাম বানাতে গিয়েও হাত-পা অর্থবোধকভাবে নাড়ানোর কৌশল বুঝতে পারছিল মানুষ। এভাবেই, সময়ের সাথে সাথে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল ভাষা।
একটা সময়, হয়তো রাতের বেলা আগুনের পাশে বসে মজা করে প্রাণীদের ডাক নকল করতে গিয়ে, বা নিজেদের মতো করে কিছু বোঝাতে গিয়ে মানুষ গাইতে শিখেছে। টের পেয়েছে, গলার তাল-লয় নিয়ন্ত্রণ করে অর্থবোধক ধ্বনিকে আরো সুমধুর করে তোলা যায়।
এই গান গাওয়াটার খুব বড় একটা ভূমিকা আছে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। সাধারণ বাক্যে ‘আমরা’ বা দলগত বোধটা সেভাবে প্রকাশ পায় না। গানে সেটা সহজেই করা যায়। একজন গাইতে থাকলে বাকিরা গলা মেলাতে পারে। এটাও আসলে আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির অংশ। এখনও সেজন্যই গান শুনলে আমরাও গলা মেলাই, মেলাতে চাই। শব্দ করে না হলেও মনে মনে গেয়ে উঠি একই বাক্য।
ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডনের নৃতত্ত্ববিদ জেরোম লুইস মনে করেন, এভাবেই গড়ে উঠেছে ভাষা। আর, এই প্রস্তাবনা সত্যি হলে এটি যেমন ভাষা ও গানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিতে পারবে, তেমনি বলতে পারবে এদের উৎপত্তির সময়কালও। আর, এই উৎপত্তির সময়টা পেলে দিনে দিনে ভাষার ওপরে কী প্রভাব পড়েছে এবং ভাষা কীভাবে বদলেছে- তার একটা মোটামুটি হিসেব আমরা দাঁড় করাতে পারব।
শব্দ হয়তো ফসিল রেখে যায় না, রেখে যায় না কোনো চিহ্ন। কিন্তু এত বছর পরে হলেও, আমরা এর ইতিহাস লেখার সূত্র খুঁজে পেয়েছি। হয়তো আরো কিছুটা সময় লাগবে, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই লিখে ফেলতে পারব ভাষার ইতিহাস। মানুষের ইতিহাসের ওপরে এর প্রভাব ও সময়ের বাঁকে বাঁকে এর দিক বদল। আসলে, বিজ্ঞানীরাও সেজন্যই ভাষার গল্পটা বোঝার চেষ্টা করে গেছেন নিরন্তর।
কারণ, ভাষার ইতিহাস ছাড়া মানুষের ইতিহাস কোনোভাবেই পূর্ণতা পায় না।



