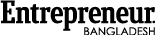আগে যে ভাবে লড়াই করার কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গাঁধীর মতো মানুষ, সেই ভাবনার আদৌ আর কোনও অর্থ আছে কি না, সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।
গোটা পৃথিবীতেই শাসকেরা ক্রমশ দাঁত-নখওয়ালা স্বৈরাচারী হয়ে উঠছেন। মানবাধিকার লঙ্ঘন করা উচিত নয়, গণতন্ত্রে আপনি বিচার-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, অপর দলের সাংসদকে প্রলুব্ধ করা অনৈতিক ইত্যাদি কথা অনেকেই নানা ভাবে বলছেন— তবে এ সব ক্রমশই অর্থহীন কথার কথা হয়ে উঠছে। নৈতিকতা ও অনৈতিকতা, এই দুই বিপরীত পরস্পর সম্পর্কিত কাঠামোর মধ্যে যাঁরা থাকেন, তাঁদের কাছে এই সব কথার মানে আছে। যাঁরা নৈতিকতার বোধশূন্য, তাঁরা কিন্তু ভয়ঙ্কর ক্ষমতার অধিকারী। নৈতিকতা-বিবর্জিত মানুষ বলতেই পারেন: “মানবাধিকার! সে আবার কী? বিচার-ব্যবস্থাকে তো আমরা নিয়ন্ত্রণ করবই।” যেমন তেমন করে দল ভাঙানোই ক্ষমতা দখলের উপায়। নীতিবাক্য তাঁদের কাছে ন্যাকামি আর বোকামি। সুতরাং, আগে যে ভাবে লড়াই করার কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গাঁধীর মতো মানুষ, সেই ভাবনার আদৌ আর কোনও অর্থ আছে কি না, সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস কাছে এলে মনে হয়, আদৌ কি তাঁর ভাল ভাল কথার এ কালে আর কোনও মানে থাকছে? রবীন্দ্রনাথ সামাজিক ভাবে এবং গাঁধী রাজনৈতিক ভাবে অহিংসা-ধর্মের প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অভিমত ছিল, গাঁধীও সমাজ সংগঠনের কথা ভেবেছিলেন, তাতে অহিংসার কথা নানা ভাবে প্রকাশিত।
১৯২০। ইয়ং ইন্ডিয়া-তে প্রকাশিত হল গাঁধীর রচনা ‘দ্য ডকট্রিন অব দ্য সোর্ড’। লেখাটিতে তিনি অহিংসা-ধর্মের স্বরূপ ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর লেখা থেকে অহিংসা-ধর্মের প্রাথমিক শর্তগুলিকে ধাপে ধাপে সাজিয়ে দেওয়া চলে। তাঁর অভিমত, অহিংসার সামর্থ্য আসে অনমনীয় মানসিক শক্তি থেকে। কেবল প্রাচীন ঋষিরাই যে এই ধর্ম পালনের অধিকারী ছিলেন তা নয়, সাধারণ মানুষও এর অধিকারী। প্রাচীন কালে আত্মোৎসর্গের যে দর্শন সুপ্রচলিত ছিল, তারই আধুনিক রূপ হল অহিংস সত্যাগ্রহীদের আত্মনিগ্রহ। সচেতন ভাবে বিরোধী শক্তির সম্মুখে যদি সত্যাগ্রহীরা সমবেত ভাবে অহিংস আত্মনিগ্রহ করেন, তা হলে এক সময় সেই আত্মনিগ্রহের অভিঘাতে শাসকের মন যায় বদলে। গাঁধীর স্থির বিশ্বাস ছিল, যদি যথেষ্ট সংখ্যক সত্যাগ্রহী সচেতন ভাবে অহিংস প্রতিরোধ করেন, তা হলে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হবে। ১৯২০ সালে গাঁধী যখন এ কথাগুলি লিখছিলেন, তখন জালিয়ানওয়ালা বাগের স্মৃতি দগদগে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ন্যায়সঙ্গত ক্রোধের প্রকাশ ঘটিয়ে নাইটহুড ত্যাগ করেছেন। তাই অনেকেরই মনে হয়েছিল, গাঁধীর এই অহিংসা-ধর্ম কার্যকর হবে না। তবে সত্যাগ্রহীর আত্মনিগ্রহের কার্যকর রূপ পরবর্তী কালে নিজের চোখে দেখেছিলেন সাংবাদিক ওয়েব মিলার। লবণ সত্যাগ্রহের দৃশ্য তিনি ভুলতে পারেননি। পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে ২০টি দেশে ঘোরা এই মানুষটি সন্ত্রাস, গৃহযুদ্ধ, লড়াই-প্রতিরোধ কম দেখেননি। কিন্তু এমন অহিংস লড়াই! ওয়েব মিলারের বিবরণ দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।
১৯২২। রবীন্দ্রনাথের নাটক ‘মুক্তধারা’ প্রকাশিত হল। এ নাটক গভীর ভাবে রাজনৈতিক। প্রাকৃতিক জলধারার উপরে বাঁধ দিয়ে শিবতরাইয়ের প্রজাদের জলের অধিকার খর্ব করতে চান শাসক, আদায় করতে চান জল কর। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে পাড়ায় পাড়ায় লোকেদের জাগিয়ে তোলেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। সেই ধনঞ্জয় কিন্তু বলেন অহিংস মন্ত্রের কথা। কী বলেন ধনঞ্জয়? গণেশ বলেছিল তাঁকে, “চণ্ডপালের দণ্ডটা খসিয়ে দিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।” উত্তরে ধনঞ্জয় বলেন, “মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস নে?” এই যে ‘মার কাকে না বলে’, এ অহিংসার সাধনা। “মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগছে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।” ধনঞ্জয় জানেন, তিনি যা বললেন তা গণেশদের উপলব্ধি করতে হবে, সচেতন ভাবে এই ‘না মার’-এর বোধ তৈরি না হলে বিপ্লব ব্যর্থ। ধনঞ্জয় বলেন, “তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভয় করিস, আমি মারতে চাই নে তাই ভয় করি নে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে থাকে।” ১৯২০ সালে প্রকাশিত গাঁধীর লেখার সঙ্গে ১৯২২ সালে লেখা রবীন্দ্রনাটকের এই ধনঞ্জয়-দর্শনের অনেক সাদৃশ্য। রবীন্দ্রনাথ আর গাঁধীর নানা মতভেদ ছিল, তবে এই অহিংসা-ধর্মের বিশ্বাসে কোথাও তাঁদের ধাতুগত মিল ছিল। তাই শেষ অবধি নানা মতভেদের পরেও তাঁরা পরস্পরের কাছে থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এক ভাবে রবীন্দ্রনাথ গাঁধীকেই দিয়ে গিয়েছিলেন।
এই অহিংসা ধর্ম কী ভাবে রাজনৈতিক দিক দিয়ে কার্যকর হয়, তা পরবর্তী কালে বিশ্লেষণ করেছিলেন নির্মলকুমার বসু, তাঁর ‘গভর্নমেন্ট এবং গান্ধীবাদ’ প্রবন্ধে। নির্মলকুমার বসু গাঁধীপ্রেমী হলেও তাঁর অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। গাঁধীর নানা কাজের সমালোচনা করেছিলেন অকপটে, বাপুও অকপট সমালোচনা সহ্য করতেন। না হলে সত্যের সঙ্গে কেমন করে বোঝাপড়া হবে! নির্মলকুমার লিখেছিলেন, “প্রতিরোধকালে সত্যাগ্রহীকে সর্ববিধ আঘাতের মধ্যেও [গাঁধী] অটল থাকিতে বলিতেন। নিজের অত্যাচারের কোনও ফল না ফলিলে বিস্ময় জাগিবে; তখন অত্যাচারী প্রতিপক্ষ সত্যাগ্রহীর সহিত আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন— ইহাই গান্ধীজীর আশা ছিল।” সে আশা বোধ করি রবীন্দ্রনাথও মনে মনে পোষণ করতেন, ভাবতেন মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। ধনঞ্জয় বৈরাগী যে না-মারের পন্থার কথা বলেছিলেন, সে তো এক রকম ভাবে এই বিশ্বাসকেই প্রতিষ্ঠা দেয়।
কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ, গাঁধী যে মারহীন আত্মশক্তির কথা ভাবছিলেন, তা এখন কি কার্যকর হবে? এই পৃথিবীর নীতিবোধ-বিবর্জিত স্বৈরাচারীদের মনে রবীন্দ্রবাণী বা গাঁধীবচন কি নিতান্তই উপহাসের সামগ্রী নয়? তা হলে কি গাঁধী, রবীন্দ্রনাথকে আমরা ফেলে দেব? এমন এক প্রশ্নের মুখে এসে আবারও তাঁদের লেখা নতুন করে পড়তে হয়। অন্য পথের কথাও তাঁরা বলেছিলেন। গাঁধী নিজেকে প্রায়োগিক কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন আদর্শবাদী বলে মনে করতেন। ‘প্র্যাকটিকাল আইডিয়ালিস্ট’-এর ধর্ম কী? তার খোঁজ খানিকটা পাওয়া যায় তাঁর ১৯৩৩ সালে হরিজন-এ প্রকাশিত একটি লেখায়। সেখানে তিনি তাঁর পাঠক ও গুণগ্রাহীদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, তাঁর আগের ভাবনা ও পরের ভাবনার মধ্যে তাঁরা যেন সামঞ্জস্য আশা না করেন। তিনি সত্যানুসন্ধানী, সত্যের টানেই নতুন জিনিস শেখেন, পুরনো জিনিস বাতিল করে দেন। নিজেকে স্ববিরোধহীন সামঞ্জস্যপূর্ণ মানুষ হিসেবে প্রমাণ করার কোনও দায় তাঁর নেই। এ প্র্যাকটিকাল আইডিয়ালিস্টেরই কথা।
নির্মলকুমার বসুর লেখা প্রবন্ধ সঙ্কলন গণতন্ত্রের সঙ্কট-এর প্রচ্ছদে তিনি গাঁধীর অন্য রকম কথা উদ্ধৃত করেছিলেন, বাংলায়। গাঁধী বলেছেন, “ম্যায় নির্দয় হুঁ— আমার হৃদয়ে দয়া মায়া নাই, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যদি কিছু লোকক্ষয়ও হয় আমি নীরবে সহ্য করিব।” এ কথা ভাবার দরকার নেই যে স্বৈরাচারী নৈতিকতার বোধহীন মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে গাঁধী একই পথ গ্রহণ করতেন। মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিলে তাঁর লড়াইয়ের পথও হয়তো যেত বদলে।
আর রবীন্দ্রনাথ? ‘মুক্তধারা’ নাটকের দু’বছর পরেই তিনি লিখলেন ‘রক্তকরবী’। সে নাটকে নানা ঘটনাক্রমে স্বৈরাচারী দম্ভী শাসকের মন বদলে গেল বটে, কিন্তু মন বদল হল না বাকিদের। ক্ষমতাতন্ত্রের সেই ভয়ঙ্কর ফাঁস থেকে মুক্তি পেতে গেলে লড়তে হবে, সে নাটক তাই শেষ হল লড়াইয়ের কথায়। কাজেই রবীন্দ্রনাথও নৈতিক কাঠামোর মধ্যে অহিংসা-ধর্মের গুরুত্ব স্বীকার করলেও প্রয়োজনে যে সংঘাতের পথে যেতে হয়, তা অস্বীকার করতেন না।
আজ যখন গণতন্ত্রের সঙ্কট গভীরতর হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে, তখন আমরা রবীন্দ্রনাথ বা গাঁধীকে ফেলে দেব না। বরং সংঘাতের সার্বিকতা যেখানে অস্বীকার করা যায়, সেখানে তা অস্বীকার করে ‘না-মার’এর অহিংস দর্শনে ব্রতী হওয়ার চেষ্টা করব। যেখানে উপায় নেই সেখানে প্রতিরোধের অন্য পথ ছাড়া গত্যন্তর নেই। গণতন্ত্রের সঙ্কট নইলে কাটবে না।
বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী